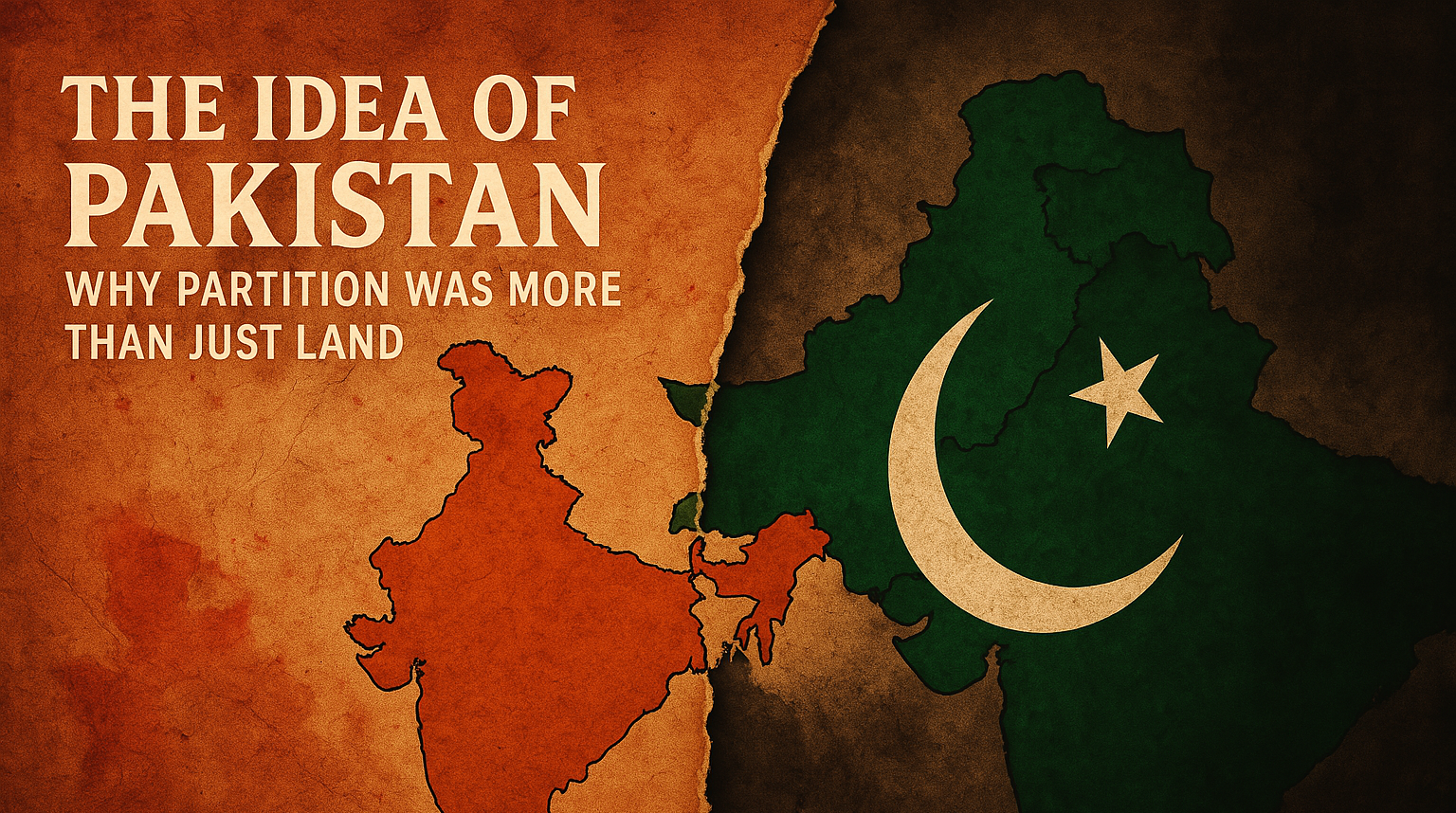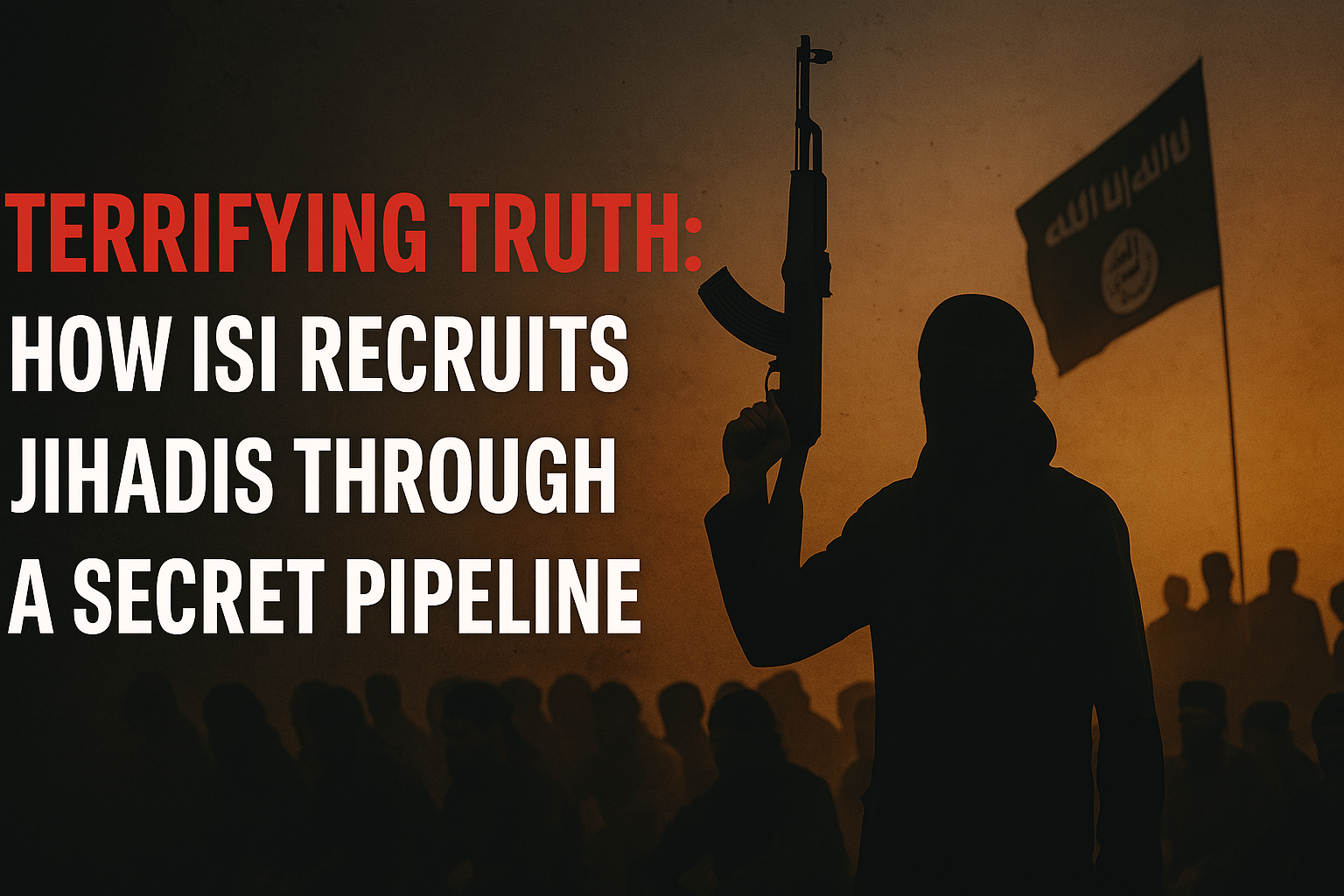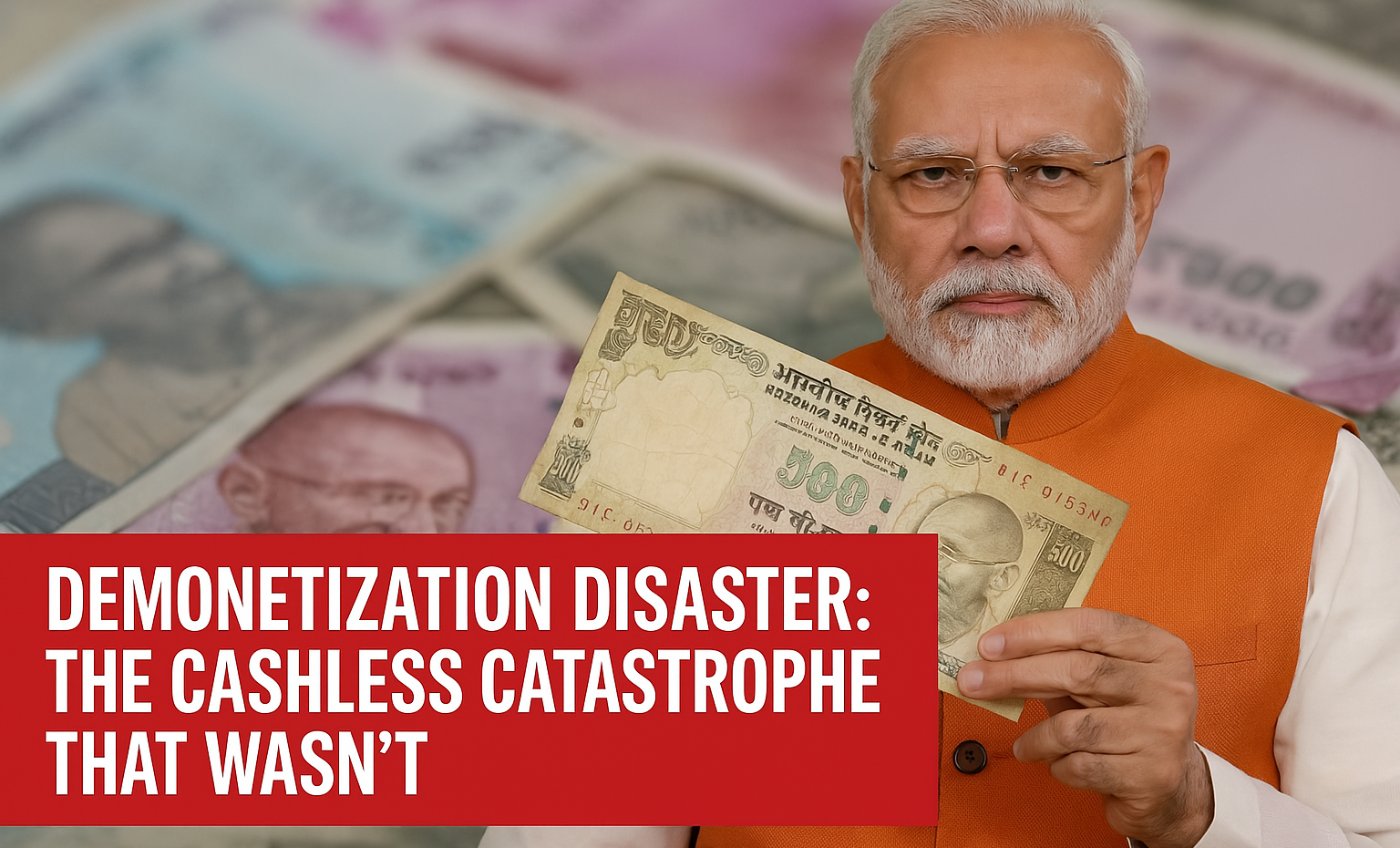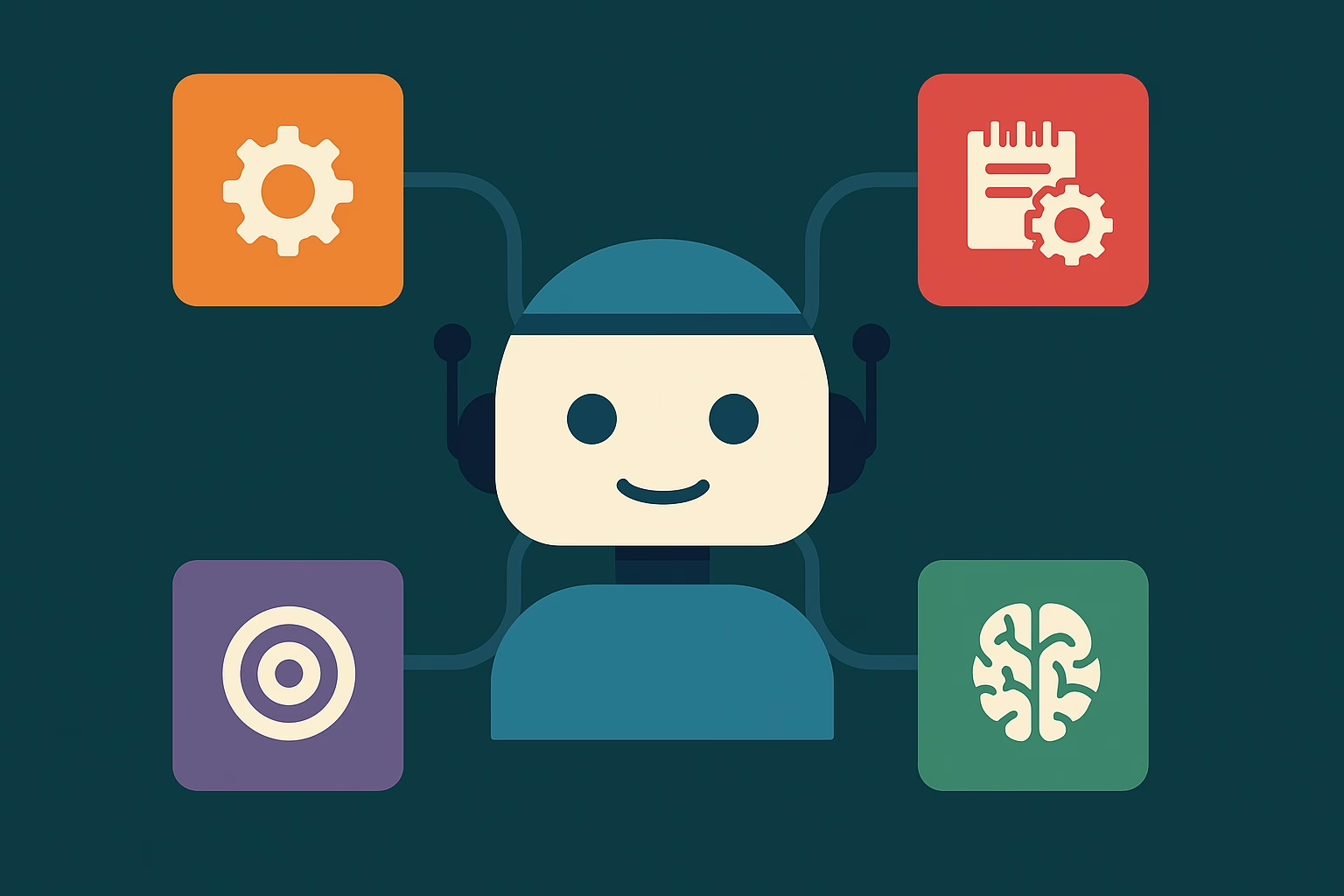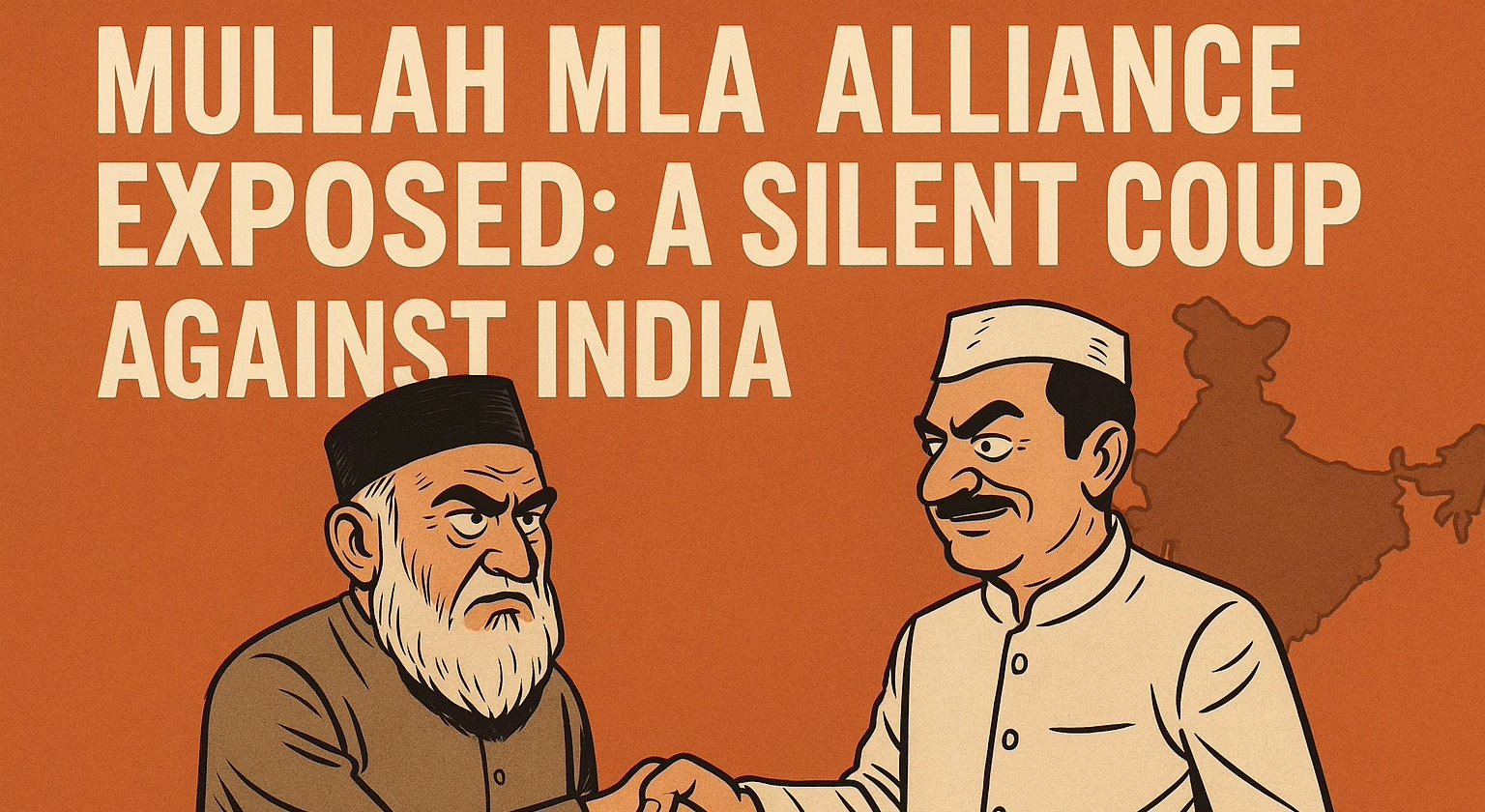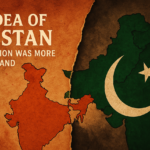১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা তাদের ব্যাগ গুছিয়ে উপমহাদেশে এক দাগ টেনে দিয়ে পাকিস্তানের ধারণার জন্ম দেয়—এটি শুধু জমির বিভাজন ছিল না। এটি একটি সীমারেখা নয়, এটি ছিল একটি রক্তরেখা, একটি বিশ্বাসের কাঠামো, একটি সমান্তরাল জগতের সূচনা—যেখানে ভারতের অস্তিত্বকেই একটি মহাজাগতিক ভুল হিসেবে দেখা হয়।
বিভাজন ছিল না শুধুই একটি ভূ-রাজনৈতিক ঘটনা। এটি একটি এমন ধারণার জন্ম দেয়—যা এতটাই শক্তিশালী এবং বিষাক্ত যে, এটি আজও ডুরান্ড এবং র্যাডক্লিফ রেখার বহু দূরেও ছড়িয়ে পড়ে।
এই বিশ্বাসব্যবস্থা, যাকে দুই জাতি তত্ত্ব হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে, কেবল মুসলমানদের জন্য নতুন একটি রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। এটি উপমহাদেশের হাজার বছরের সভ্যতাগত ঐক্যকে চিরতরে ছিন্ন করার প্রচেষ্টা ছিল এবং একটি আদর্শগত যুদ্ধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল—যা আজও চলছে, ভারতের ভেতরে, দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতেও।
“সত্য হলো, জাতিগুলো জমির উপর নয়, গল্পের উপর গঠিত হয়। আর পাকিস্তানের ধারণা এমন একটি গল্প যা মিথ্যা দিয়ে শুরু হয়েছে, কল্পনার পালে হাওয়া পেয়েছে, আর বিভ্রান্তির ভূতের মতো তাড়া করে চলেছে।”
পাকিস্তানের ধারণা: দুই জাতি তত্ত্বের ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তি
হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পূর্ণ আলাদা জাতি হিসেবে বিবেচনা করার তত্ত্বটি দিল্লির বাজারে বা পাঞ্জাবের কৃষিজমিতে জন্মায়নি। এটি জন্ম নিয়েছিল মুসলিম অভিজাতদের অন্দরে—যাঁরা ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় প্রভূত সুবিধা ভোগ করতেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার পর, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমতা মেনে নেওয়া তাঁদের কাছে ছিল এক অসহনীয় ভবিষ্যৎ।
অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ, সাধারণ মানুষের বাস্তবতা নয়, বরং অভিজাতদের দুশ্চিন্তা থেকে চালিত হয়ে, এই দুই জাতি তত্ত্বকে একধরনের সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। বাস্তবে, এটি ছিল একটি আগাম হামলা। একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, যারা তাদের অতিরিক্ত প্রভাব হারানোর আশঙ্কায় ভুগছিল, ধর্মীয় পরিচয়কে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল ক্ষমতা পাওয়ার জন্য। এটি ছিল রাজনীতির দাবার ছক উল্টে ফেলার মতোই এক কৌশল।
কিন্তু এই তত্ত্বটির মূলে ছিল এক গুরুতর ভুল। এটি শতাব্দীর সহাবস্থান, ভাষাগত মিল, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছিল—যেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে মিলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এটি একটি বহুত্ববাদী সভ্যতাকে একটি দ্বৈত বিভাজনে নামিয়ে এনেছিল—যার ফল ছিল রক্তাক্ত।
জিন্নাহ, যিনি এক সময় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ছিলেন, হঠাৎ করেই মুসলিমদের মুক্তিদাতা হয়ে উঠলেন। ১৯১৬ সালে যিনি পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন, তিনি ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে বললেন, মুসলমানরা “একটি জাতি… যাদের নিজেদের প্রথা, ধর্ম এবং বীর রয়েছে।” এটি ছিল এক চূড়ান্ত পরিচয় সংকট—“আমরা একসাথে খেলতে পারছি না, তাই নিজের খেলার মাঠ তৈরি করবো, যতই সেটা বালির উপর হোক।”
সব মুসলমান এটি চাননি
একটি মিথ ভেঙে দিই: বেশিরভাগ ভারতীয় মুসলমান দেশত্যাগ করেননি।
প্রায় ১০–১২ মিলিয়ন মানুষ মাত্র সীমান্ত পার হয়েছিল। বাকিরা—৩০ মিলিয়নেরও বেশি মুসলমান—ভারতে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। যদি পাকিস্তান সত্যিই মুসলমানদের জন্য প্রতিশ্রুত ভূমি হতো, তাহলে বেশিরভাগ মুসলমান কেন “হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ” দেশে রয়ে গেলেন?
সুস্পষ্ট যে, পাকিস্তানের ধারণা ছিল না একটি সামগ্রিক মুসলিম আকাঙ্ক্ষা—এটি ছিল কিছু নেতার রাজনৈতিক বিভ্রম, যারা প্রতিযোগিতা ছাড়াই শাসন করতে চেয়েছিলেন।
একটি “না”-এর ভিত্তিতে গঠিত দেশ
প্রায় সব দেশই কোনো ইতিবাচক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত—স্বাধীনতা, ঐক্য, ন্যায়বিচার।
পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল “বিরোধিতা”-র উপর—ভারতের বিরুদ্ধতা।
তাদের পাঠ্যপুস্তকে শেখানো হতো কীভাবে কিছু গড়ে তুলতে হয় না, বরং কীভাবে ঘৃণা করতে হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পাকিস্তানিদের শেখানো হয়েছে যে হিন্দুরা তাদের চিরশত্রু, ভারতের ইতিহাস শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালে, আর তার আগের সব কিছুই ছিল ইসলামী।
পাকিস্তানি পাঠ্যক্রমে:
- আকবরকে দেখানো হয় বিভ্রান্ত মুসলমান হিসেবে, সহনশীল শাসক হিসেবে নয়।
- হিন্দুধর্মকে বলা হয় কুসংস্কার।
- বাংলাদেশ ছিল না (যতক্ষণ না পাকিস্তান নিজেই সেটিকে নিশ্চিহ্ন করতে গিয়ে হারায়)।
- পাকিস্তান শুধু ভারতের অংশ থেকে আলাদা হয়নি। এটি তথ্য থেকেও আলাদা হয়েছে।
ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ফ্রাঙ্কেনস্টাইন
পাকিস্তানের ধারণার একটি অদ্ভুত দিক আছে—এটি একটি অতল গহ্বর।
হিন্দুদের বাদ দেওয়ার পর, পরবর্তী টার্গেট ছিল আহমদিয়া, শিয়া, খ্রিস্টান ও শিখদের মতো সংখ্যালঘুরা। পাকিস্তান ক্রমাগত “বিশুদ্ধতার” মানদণ্ড পরিবর্তন করে:
- ১৯৭৪ সালে আহমদিয়াদের অ-মুসলিম ঘোষণা করা হয়।
- শিয়ারা নিয়মিত বোমা হামলার শিকার।
- আজ হিন্দুদের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১.৫%।
এটাই ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতে গঠিত একটি রাষ্ট্রের পরিণতি—নিজেকেই খেয়ে ফেলে। এটি যেন একটি সাপ, নিজের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে নিজের লেজ খেয়ে নিচ্ছে।
মনের মধ্যে পাকিস্তান: কেন বিভাজন শেষ হয়নি
বুঝে রাখুন: ভৌগোলিক বিভাজন হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। কিন্তু আদর্শগত বিভাজন আজও অব্যাহত।
শাহিনবাগ থেকে পাথর নিক্ষেপকারী দল পর্যন্ত, দাঙ্গার উপর নির্বাচিত ক্ষোভ থেকে উগ্রপন্থীদের প্রশংসা পর্যন্ত—ভারতে আজও এক ক্ষুদ্র কিন্তু বিপজ্জনক স্রোত রয়েছে যারা “মনস্তাত্ত্বিক পাকিস্তানে” বিশ্বাস করে।
এটিকে বলা যায়—“মনের মধ্যে পাকিস্তান।” এটি কোনো সবুজ পতাকা নয়, বরং “ধর্মনিরপেক্ষতা”-র মুখোশ পরে আসে এবং ভিক্টিমহুড কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে।
ব্যর্থতার এক ট্র্যাজিকমেডি
পাকিস্তান ব্যর্থ হয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রতিটি সূচকে:
- গণতন্ত্র? সেনাশাসনই স্বাভাবিক।
- অর্থনীতি? ঋণ ও প্রার্থনার উপর নির্ভর।
- শিক্ষা? যুক্তির চেয়ে উগ্রতাকে প্রাধান্য দেয়।
- কূটনীতি? এমনকি OIC-ও বিব্রত।
তবে একটি জায়গায় তারা শ্রেষ্ঠ—ঘৃণা রপ্তানি।
সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো পেনশন পায়। ঘৃণা তাদের GDP। গজওয়া-এ-হিন্দ তাদের স্টার্টআপ আইডিয়া।
পাকিস্তানের ধারণা: কেন এটি আজও গুরুত্বপূর্ণ
পাকিস্তান যদি শুধু আরেক প্রতিবেশী হতো, তাহলে চলেই যেত। কিন্তু এটি একটি কেস স্টাডি—যখন ঘৃণাই হয় জাতীয় ধর্ম।
এটি একটি আয়না, যা আমাদের দেখায়—কি হতে পারে যদি আমরা এই আদর্শিক যুদ্ধকে অবহেলা করি।
ভিক্টিমহুড অর্থনীতি এবং স্থায়ী অবরোধ মানসিকতা
পাকিস্তানি প্রশাসন—বেসামরিক, সামরিক ও ধর্মীয়—ভিক্টিমহুডকে একটি অর্থনীতিতে রূপান্তর করেছে। শীতল যুদ্ধের সময়, আমেরিকার ডলার নিয়ে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল (পরবর্তীতে ওসামা বিন লাদেনকেও আশ্রয় দিয়েছিল)। পরবর্তীতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-এ উভয় পক্ষকেই খেলেছিল।
এখন এই ভিক্টিম ন্যারেটিভ ভারতের কিছু অংশেও প্রতিধ্বনি তৈরি করেছে।
- প্রতিটি পুলিশ এনকাউন্টার হয়ে ওঠে “উইচ হান্ট”।
- প্রতিটি আইনি সংস্কার হয় “ইসলামোফোবিক”।
- প্রতিটি বিতর্ক হয়ে যায় “অত্যাচার”।
যে ন্যারেটিভ পাকিস্তান বিশ্বজুড়ে সহানুভূতি অর্জনের জন্য ব্যবহার করে, সেটিই আজ ভারতে ব্যবহার করছে তাদের আদর্শিক সহযোগীরা—অনেক সময় তথাকথিত “লিবারেল বুদ্ধিজীবীদের” সমর্থনে।
উপসংহার: কেন এই আদর্শিক যুদ্ধ স্পষ্টভাবে লড়তে হবে
পাকিস্তানের ধারণা কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। এটি একটি জীবন্ত আদর্শ—যা পাঠ্যপুস্তকে, টিভি বিতর্কে, জুমার খুতবায়, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভে, এমনকি আমাদের প্রতিবেশীদের মনেও বাস করে।
শুধু পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সমালোচনা করলেই হবে না। আমাদের বুঝতে হবে, উন্মোচন করতে হবে—পাকিস্তান নামক ধারণাকে। এটি বিভাজন, অস্বীকার ও ধ্বংসের উপর গড়ে উঠেছে। একটি আদর্শ যা নিজের জনগণের প্রতিও বিশ্বস্ত থাকতে পারেনি—বাংলাদেশের বিচ্ছেদ, বেলুচদের নিপীড়ন, পশতুনদের বিশ্বাসঘাতকতা, শিয়া ও আহমদিয়াদের গণহত্যা—এগুলি প্রমাণ করে যে, এমন একটি আদর্শ বিশ্বশান্তি বা বহুত্ববাদকে সম্মান জানাবে, এমন আশা রাখা বাতুলতা।
ভারতকে তার নিজস্ব গল্প আবার নিজের ভাষায় বলতে হবে—বিনা দ্বিধায়, বিনা ক্ষমাপ্রার্থনায়।
একটি গল্প যা ঘৃণার নয়, বরং ইতিহাসের সত্যের উপর ভিত্তি করে। একটি গল্প যা বাস্তবতাকে অসহিষ্ণুতা হিসেবে ভুল না করে।
কারণ একটি আদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে, প্রথমে তাকে সনাক্ত করতে হয়।
পরিষ্কারভাবে বুঝে নিন: বিভাজন একবারের ঘটনা ছিল না। এটি ছিল একটি আদর্শিক সংঘর্ষের সূচনা।
এবং সেই যুদ্ধ—একটি ঐক্যের উপর গড়া সভ্যতাগত রাষ্ট্র বনাম বর্জনের উপর গঠিত ব্যর্থ রাষ্ট্র—আজও চলছেই।
এবং যতক্ষণ না আমরা “পাকিস্তান”-এর ধারণাকে পরাস্ত করি, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতের ঐক্যের গল্প থাকবে আক্রমণের লক্ষ্য।